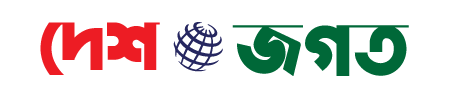
রেমিট্যান্স-রফতানির প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রিজার্ভ বাড়ছে না, স্থবির বিনিয়োগ ও ঋণ পরিশোধে ক্ষয়

রেমিট্যান্স-রফতানির প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রিজার্ভ বাড়ছে না, স্থবির বিনিয়োগ ও ঋণ পরিশোধে ক্ষয়
দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত ১১ মাস ধরে ২০ বিলিয়ন ডলারের আশপাশে ওঠানামা করছে। অথচ চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ১১ মাসে রেমিট্যান্স ও রফতানি আয়ে প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে প্রায় ২৫ ও ১০ শতাংশ হলেও রিজার্ভে তার প্রতিফলন নেই। বরং একই সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত কমেছে ০.৮২ বিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের ১৫ জুন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড বিপিএম৬ অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২০.৮৬ বিলিয়ন ডলারে, যেখানে অর্থবছরের শুরুতে (২০২৪ সালের ১ জুলাই) এই পরিমাণ ছিল ২১.৬৮ বিলিয়ন ডলার।
প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ গত ১১ মাসে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ৬৫৬ মিলিয়ন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫,৬৩৮ মিলিয়ন ডলার বেশি। রফতানি খাতেও একই সময়ের মধ্যে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার বাড়তি আয় সত্ত্বেও রিজার্ভ বাড়ছে না, কারণ বিদেশি বিনিয়োগ, অনুদান ও ঋণ প্রবাহে এসেছে বড় ধরনের স্থবিরতা।
চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কমেছে ৩৭ কোটি ডলার, বিদেশি অনুদান কমেছে ১৮৬ কোটি ডলার, এবং মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ কমেছে ১৩৬ কোটি ডলার। শুধু এই তিনটি খাতেই বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ কমেছে ৩.৬১ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে আমদানি ব্যয় বেড়েছে ২.৪২ বিলিয়ন ডলার। পাশাপাশি বিদেশি ঋণ পরিশোধ, সেবা খাতে ব্যয় এবং বকেয়া ঋণপত্রের দায় মেটানোয় রিজার্ভ থেকে বড় অঙ্কের মুদ্রা বেরিয়ে গেছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানিয়েছেন, জুন মাসেই আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও জাইকা থেকে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তবে তিনি স্বীকার করেন, গত ১১ মাসে বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অঙ্কের বিদেশি ঋণ ও দায় পরিশোধ করেছে—যা না হলে রিজার্ভ আরও ৩-৪ বিলিয়ন ডলার বেশি হতে পারতো।
এদিকে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে (বিওপি) ঘাটতি কমে এসেছে অনেকটা। চলতি অর্থবছরের এপ্রিল শেষে ঘাটতি নেমে এসেছে মাত্র ৬৬ কোটি ডলারে, যেখানে গত বছর ছিল ৬৫৭ কোটি এবং তার আগের বছর ছিল ৮২২ কোটি ডলার। এর ফলে রিজার্ভ থেকে আগের মতো বিপুল পরিমাণ ডলার বিক্রি করতে হচ্ছে না।
তবে জুনের শুরুতে রেমিট্যান্স প্রবাহে দেখা গেছে হঠাৎ ভাটা। ১ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত এসেছে মাত্র ১১৪৯ মিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩০ শতাংশ কম। যদিও বিশ্লেষকরা বলছেন, এই পতন ক্ষণস্থায়ী হতে পারে।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, রেমিট্যান্স ও রফতানি আয় বাড়লেও বিদেশি বিনিয়োগ ও ঋণ প্রবাহ স্থবির থাকলে রিজার্ভে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. মুস্তাফা কে মুজেরীর মতে, শুধু আয় বাড়ালেই চলবে না, বরং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত না হলে রিজার্ভ পুনরুদ্ধারও কঠিন হবে।
গত ১১ মাসে রিজার্ভের ওঠানামায় দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য তারতম্য। জুলাইয়ে রিজার্ভ ছিল ২১.৬৮ বিলিয়ন ডলার, যা আকুর দায় পরিশোধের পর নেমে আসে ২০.৪৯ বিলিয়নে। এপ্রিলের শেষে তা আবার বেড়ে দাঁড়ায় ২২ বিলিয়নে, তবে মে মাসে আবার কমে ২০ বিলিয়নে। ঈদের আগে ৪ জুন ছিল ২০.৭৬ বিলিয়ন ডলার এবং ঈদের পর ১৫ জুন তা দাঁড়ায় ২০.৮৬ বিলিয়ন ডলারে। যদিও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবে এই মজুত ২৬.১৪ বিলিয়ন ডলার, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী নয়।
সবমিলিয়ে, রিজার্ভে স্থিতিশীলতা আংশিক ফিরে এলেও, তা দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখতে প্রয়োজন বহুমুখী কৌশল, বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ঋণ সহায়তা এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা।
Deshjogot News